জসীম উদ্দীন [ Poet Jasimuddin ] : বাংলা পল্লীগানের অমর স্রষ্টা গীতিকবি জসীম উদ্দীনের লেখনীতে পল্লীবাংলার সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা, হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ তাঁর প্রস্ফুটিত হয়েছিল বাস্তবতার নিরিখে একেবারে জীবন্ত হয়ে।
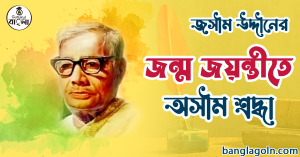
Table of Contents
গীতিকবি জসীম উদ্দীন এর জন্ম ও শৈশব:
জসীম উদ্দীন ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দের ১ জানুয়ারি ফরিদপুর জেলার তাম্বুলখানা গ্রামে নানাবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাই তো বাংলার সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে অমর হয়ে আছেন তিনি পল্লীকবি নামে।
পৈতৃক বাড়ি অম্বিকাপুরের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া পদ্মা নদীর একটি উপশাখা গ্রামের প্রাকৃতিক শোভাকে করে তুলেছিল মনোমুগ্ধকর। বাল্যকাল থেকেই গ্রামের মানুষের জীবনের সঙ্গে তাঁর ভাবুক মন মিলেমিশে একাকার হয়ে যেত। গ্রামের পাঠশালাতেই শুরু হয় তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। স্কুলশিক্ষক

পিতার সঙ্গে গ্রামের মেঠোপথ বেয়ে প্রায়ই তিনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কিংবা স্থানীয় বাজারে যাতায়াত করতেন। চলার পথে আশপাশের মাঠে বা ফসলের ক্ষেতে খেলায় মগ্ন অথবা কর্মরত কৃষক ছেলেদের দেখে কল্পনায় তাদের মতো হতে চাইতেন। পল্লীগীয়ের নিত্যদিনের সহজাত বিষয়গুলোকে হৃদয়ে ধারণ করে তাতে মাধুরী মিশিয়ে মুখে মুখে রচনা করতেন ছন্দোবদ্ধ কবিতা।
শৈশবে গ্রামের রাখাল বালক কিংবা খেয়া মাঝির কণ্ঠে গান শুনে তাঁর ভেতরে সুরের অপূর্ব খেলা দোলা দিয়ে যেত। ইচ্ছেমতো সুর তৈরি করে তৎক্ষণাৎ কথা বানিয়ে আপন খেয়ালে গলা ছেড়ে গাইতেন। তাই না দেখে লোকজন বলাবলি করত, ‘পাগলার পাগলামি উঠিয়াছে’ স্বভাবকবি জসীম উদ্দীনের এক অন্ধ দাদাজান বলতেন ‘পাগলার গান তোমরা কেউ শোনো না, কিন্তু আমি শুনি।
ওর গান একদিন দশ গ্রামের মানুষের মুখে মুখে শোনা যাবে।”
দূরদর্শী অন্ধ দাদাজানের ভবিষ্যদ্বাণী বিফলে যায়নি, সময়ের পরিক্রমায় তা সত্য প্রমাণিত হয়েছে।
![গীতিকবি জসীম উদ্দীন | বাঙালি কবি, গীতিকার, ঔপন্যাসিক ও লেখক 3 গীতিকবি জসীম উদ্দীন [ Poet Jasimuddin ]](https://banglagoln.com/wp-content/uploads/2021/11/Bangla-GOLN-27-300x157.jpg)
জসীম উদ্দীনের লেখাপড়া:
ছোটবেলা থেকে প্রকৃতি, গ্রাম, নদী, ফসল ভরা মাঠ, শরীরে ধুলোবালি মেখে খেলাধুলা করা, মুখে মুখে গান বা কবিতা রচনা করাসহ যত ধরনের পাগলামি থাক না কেন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকে কখনোই তিনি অবহেলার চোখে দেখেননি।
আর সে কারণেই পল্লীর প্রেমে মগ্ন জসীম উদ্দীন ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে ফরিদপুর জিলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। এরপর উচ্চ মাধ্যমিক পড়ার জন্য ভর্তি হয়ে ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে রাজেন্দ্র কলেজ থেকে আইএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।
প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক হওয়ায় রুটিন বাঁধা পড়াশোনার স্বাভাবিক গতি একটু যেন শ্লথ হয়ে যায়। তারপরও প্রকৃতির পাঠশালা থেকে জ্ঞানলাভ এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় মনোনিবেশ দুইয়ে মিলে গতি সঞ্চারিত হয়ে ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে অর্জন করেন স্নাতক ডিগ্রি।

রাজেন্দ্র কলেজে বিএ শ্রেণিতে অধ্যয়নকালে মাসিক ৭০ (সত্তর) টাকা বৃত্তি পেয়ে অধ্যাপক ড. দীনেশচন্দ্র সেনের লোকসাহিত্য সংগ্রহের বিভিন্ন কার্যক্রমে উৎসাহের সঙ্গে কাজ করেন জসীম উদ্দীন।
সে সময় ঢাকার মানিকগঞ্জের কৃতী সন্তান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. দীনেশচন্দ্র সেন এবং রামতনু লাহিড়ী বিভিন্ন সংগ্রাহকের সহযোগিতায় ময়মনসিংহ ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা সংকলিত করে এক ঐতিহাসিক মহান দায়িত্ব পালন করছিলেন।
ঋদ্ধ এই কাজে সম্পৃক্ত হয়ে গ্রামবাংলার সৌন্দর্য, সাহিত্য, লোকবৃত্ত ইত্যাদির সঙ্গে যেন নতুন করে এক নিবিড় পরিচয়ের সুযোগ আসে জসীম উদ্দীনের। বিএ পাশ করার পর নিজেকে আরো শানিত করতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন।
জসীম উদ্দীনের কবিজন্ম:
ছাত্রাবস্থায়ই তাঁর বিখ্যাত ‘কবর’ কবিতাটি তৎকালীন সমৃদ্ধ পত্রিকা কল্লোলে প্রকাশিত হয়।
অল্প সময়ের মধ্যেই আধুনিক কবিতার অঙ্গনে স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর হিসেবে স্বীকৃতি পান কবি জসীম উদ্দীন। লোকসাহিত্য-গবেষক অধ্যাপক ড. দীনেশচন্দ্র সেনের পৃষ্ঠপোষকতায় ‘কবর’ কবিতাটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ম্যাট্রিকুলেশন শ্রেণির পাঠ্য হিসেবে বাংলা সিলেবাসে সংকলিত হয়।
আর এ সময়েই তিনি বিশিষ্ট পল্লীকবি হিসেবে পাঠকসমাজে সুপরিচিত হয়ে ওঠেন।
এরপর ড. দীনেশচন্দ্রের অধীনে ১৯৩১ থেকে ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পল্লীগীতি সংগ্রাহক এবং রামতনু লাহিড়ীর রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে কর্মরত ছিলেন। তখন জসীম উদ্দীন তাঁর বন্ধু বিনয়কৃষ্ণ ঘোষ ও সংগীতজ্ঞ শিল্পী আব্বাসউদ্দীন আহমদের সহযোগিতায় কলিকাতার বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পল্লীগানের বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন।
তিনজন বন্ধুর এই ক্ষুদ্র দলটির আন্তরিক প্রচার ও প্রচেষ্টায় গ্রামোফোন কোম্পানি এবং বেতার কেন্দ্রে পল্লীগানের সম্যক স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী সময়ে ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে প্রভাষক পদে নিযুক্ত হন। পাঁচ বছর অধ্যাপনা পেশায় থেকে ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সরকারের পাবলিসিটি বিভাগে কর্মকর্তা পদে যোগদান করেন।

ভারত স্বাধীন হয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের প্রচার বিভাগে অ্যাডিশনাল সং পাবলিসিটি অর্গানাইজার পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। চাকরিরত অবস্থায় তিনি সরকারি প্রতিনিধি হিসেবে আন্তর্জাতিক লোকসংগীত সভা’য় যোগদান করতে ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে আমেরিকা এবং ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে যুগোস্লাভিয়া গমন করেন।
এই সংগীত সফর দুটিতে ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে তিনি লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বক্তৃতা দেন। এর দুই বছর পর ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে তুরস্ক এবং তার তিন বছর পর ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে ‘লোকসংগীত সম্মেলনে’ যোগদানের জন্য মিয়ানমার (রেঙ্গুন) পৌছান।
বিদেশ সফরে লোকসংস্কৃতি নিয়ে তাঁর বক্তৃতা বিশ্ব সংগীতবোদ্ধা মহল ও সুধীসমাজে ভূয়সী প্রশংসিত হয়। সরকারের প্রচার বিভাগে পর্যায়ক্রমে পদোন্নতি লাভ করে উপপরিচালক পদে থাকাকালীন ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে অবসরগ্রহণ করেন। গভীর মমতা আর প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি রচনা করেন অকৃত্রিম পল্লী
জনপদের জীবন আখ্যান। পল্লীগীতি সংগ্রহের কাজে ব্যাপৃত হয়ে তিনি পৌঁছে গিয়েছিলেন পল্লীর মানুষের আবহমান সংস্কৃতির সাংগীতিক মোকামের গোপন তীর্থে। জীবনযাপনে নাগরিক বেশ থাকলেও তাঁর প্রাণের ভেতর জেগে ছিল মাটি ও মানুষের গান।

কবিতায় তিনি যেমন এঁকেছেন গ্রামীণ জনপদের নিখুঁত ছবি; ঠিক তেমনি তাঁর সৃষ্ট গানে তুলে ধরেছেন প্রাকৃতজনের প্রাণের আকুতি, বিরহ ও বেদনার এক অনবদ্য চিত্র। শৈশবে গাঁয়ের কৃষক পরিবারের সমবয়সী ছেলেদের বাপ-চাচাদের জন্য হালের ক্ষেতে নাশতা নিয়ে যেতে দেখেছিলেন।
সেখানে কলার পাতায় করে ছোটরাও বেশ মজার সঙ্গে সে নাশতায় অংশগ্রহণ করত। মাঠে বসে খাও আনন্দ থেকে বঞ্চিত কবি ভাবতেন –
“আমার বাজান যদি মাঠে লাঙ্গল বাহিতেন, তাইলে রোজ আমি আমার বন্ধুদের মতই নাস্তা লইয়া যাইতাম।’
বাল্যকালের এই আন্তরিক অনুভূতি তাঁকে অনুপ্রাণিত করে ‘বাজান চল যাই চল মাঠে লাঙ্গল বাইতে…’ বিখ্যাত পল্লীগীতিটি রচনায়। পল্লীকবির মা ছিলেন তাঁর পিতার মতোই বড় সরল প্রকৃতির। মাঝেমাঝেই তিনি নিজের শৈশবের কথা, বাড়ির কথা, গ্রামের কথা, সইদের কথা অপরূপ ভঙ্গিতে বলতেন।
ফেলে আসা বাপের বাড়ির করুণ কাহিনি মায়ের মুখে শুনতে শুনতে পুত্রের চোখে পানি ঝরত। ‘বাপের বাড়ির কথা’ কবিতায় মায়ের কাছে শোনা পল্লীজীবনের করুণ কাহিনিকে কাব্যরূপ প্রদানসহ তাঁর রচিত গানেও তা দক্ষতার সঙ্গে প্রয়োগ করেছেন।
সংগীতের গভীরে নিমজ্জমান এর সুর সঞ্চারিত প্রাণে নিজের করা সুরে সাজিয়েছেন হৃদয়ের উৎসারিত বাণী। তাঁর সৃষ্ট গানগুলোর মধ্যে শ্রোতা সমাদৃত ও জনপ্রিয় কয়েকটি উল্লেখ করা হলো –
আরে ও রঙিলা নায়ের মাঝি
আমার গলার হার খুলে নে
আমার গহীন গাঙ্গের নাইয়া
আমার সোনার ময়না পাখি
আমার হাড় কালা করলাম রে ………..
আমায় এতো রাতে কেন ডাক দিলি
আমায় ভাসাইলি রে আমায় ডুবাইলি রে
উজান গাঙ্গের নাইয়া
এই না গাঙ্গের কোন রে বন্ধু
এবার ধান কাটির কচাকচ ….…….
ও আমার দরদী, আগে জানলে ………………………….
ওকি গাঙ্গের ও কূল গেল ভাঙিয়া
ও তুই যারে আঘাত হানলি রে মনে।
ও ভাই পদ্মা নদীর মাঝিরে
ও মাঝি রে আজি ঝড় তুফানে চালাও তরী হুঁশিয়ার
ও সুজন বন্ধুরে আমার যাবার বেলায় নয়ন জলখানি
কেমন তোমার পিতা-মাতা
তোরা কে কে যাবি লো জল আনতে
নদীর কূল নাই কিনার নাইরে
নিশীথে যাইও ফুল বনে রে ভ্রমরা পেটের জ্বালায় জ্বইলা মরলাম রে……………
প্রাণ সখীরে ঐ শোন কদম্ব তলে বংশী বাজায় কে বন্ধু রঙ্গিলা, রঙ্গিলা, রঙ্গিলা রে ………………..
বাবু সেলাম বারে বার ……
মনই যদি নিবি রে বন্ধু কেনে ……………….
রাসুল নামে কে এলো মদিনায়
সোনার বরণী কন্যা সাজে নানা রঙে
বেদের মেয়ে ও মধুবালা জসীম উদ্দীনের অভূতপূর্ব কালজয়ী গীতিনাট্য। রচনা, সুরারোপ ও পরিবেশনের গুণে গীতিনাট্য দুটি বাংলার মানুষের হৃদয়ে সুগভীরভাবে রেখাপাত করে আছে। The field of the embroidered quilt শিরোনামে অনূদিত তাঁর নক্সী কাঁথার মাঠ একটি উন্নতমানের লোকজীবনভিত্তিক নৃত্যনাট্য হিসেবে দেশে-বিদেশে বহুল সমাদৃত ও প্রশংসিত হয়েছে।

বাংলা সংগীতের ভাণ্ডারে লোকসংগীতের যে সকল ধারার গান তাঁর সুনিপুণ সৃষ্টির (গীতিকার ও সুরকার) মাধ্যমে মূর্ত হয়ে উঠেছে তার মধ্যে ভাটিয়ালি, দেহতত্ত্ব, বিচ্ছেদী, রাখালি, জারি, মুর্শিদি, মরমি, বাউল, বিয়ের গান, মেয়েলি গান, বেদের গান এবং নানান কর্মসংগীত করে তুলেছে তাঁকে অবিস্মরণীয় কিংবদন্তি।
পল্লীগানের দুই প্রবাদপুরুষ (সংগীতজ্ঞ ও শিল্পী) আব্বাসউদ্দীন আহমদ ও আবদুল আলীমসহ পণ্ডিত কানাইলাল শীল, ওস্তাদ বেদার উদ্দিন আহমদ, ওস্তাদ মমতাজ আলী খান, সোহরাব হোসেন প্রমুখ খ্যাতনামা শিল্পীর কণ্ঠে তাঁর অসংখ্য গান ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।
ছোট-বড় সকলের জন্য বিভিন্ন বিষয়ের ওপর রচিত তাঁর এই গ্রন্থগুলো ইতোমধ্যেই বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।
লেখাপড়া ও চাকরির প্রয়োজনে জীবনের দীর্ঘ সময় শহরে বসবাস করলেও গীতিকবি জসীম উদ্দীনের হৃদয়জুড়ে ছিল শৈশবকাল থেকে বেড়ে ওঠা পল্লীমায়ের কোল।
গ্রামীণজীবনের নানা ঘটনা ও স্মৃতি তাঁকে বেশ আকর্ষণ করত প্রতিনিয়ত। বাংলাদেশের পল্লীর মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, ব্যথা-বেদনা, জন্ম-মৃত্যু, বিবাহ, আবেগ-ঘৃণাকে তাঁর সাহিত্য ও সংগীতে ফুটিয়ে তুলেছেন অসাধারণ নৈপুণ্যের সঙ্গে।

অবহেলিত পল্লীজীবনের উপকরণ নিয়ে নানা ধরনের গান তিনি শিক্ষিত সমাজের কাছে তুলে ধরেছেন অত্যন্ত সার্থকতার সঙ্গে। তাঁর কুশলী হাতের স্পর্শে গানগুলোর শিল্পমান কালোত্তীর্ণ হয়েছে সফলতার সঙ্গে।
যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে গ্রামবাংলার অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত শ্রেণির গান শিক্ষিত সমাজে এখন আন্তরিকতার সঙ্গে সমাদৃত ও গৃহীত হয়েছে গীতিকবি জসীম উদ্দীন নিঃসন্দেহে তাঁদের পুরোভাগের অন্যতম।
পল্লীর গান যে দেশীয় সংস্কৃতির প্রধানতম অঙ্গ সে সত্যকে পল্লীকবি তাঁর লেখা ও সুরের মধ্য দিয়ে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।
বাংলার লোকসংগীত ও গ্রামীণ সংস্কৃতিকে সার্থকতার সঙ্গে বেশ সম্মানজনক অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করে নিবেদিতপ্রাণ সংগীতজ্ঞ, গীতিকবি এবং বাংলার মানুষের অতিপ্রিয় পল্লীকবি জসীম উদ্দীন ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ মার্চ ঢাকার কমলাপুরে অবস্থিত নিজস্ব নিবাস ‘কবি ভবনে’ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।
বাংলা সংগীতের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করতে বিদগ্ধ সংগীতস্রষ্টা জসীম উদ্দীনের অবদান ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে স্বর্ণাক্ষরে।
অবিস্মরণীয় কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে তাঁকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ড ‘প্রাইড অব পারফরম্যান্স’, ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ‘ডি-লিট’ খেতাব, ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে ‘একুশে পদক’ এবং ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার ‘স্বাধীনতা পদক’ (মরণোত্তর) প্রদান করা হয়।

জসীম উদ্দীন এর কবিতা:
- অনুরোধ
- প্রতিদান
- আমার বাড়ি কবিতা
- নিমন্ত্রণ কবিতা
- নকশী কাঁথার মাঠ
- আজ আমার মনে ত না মানেরে
- আমার খোদারে দেখিয়াছি আমি
আরও পড়ুন :