বর্ণনানুক্রমে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার বর্ণনা পর্ব ১৩ – টিজেলটাল (Tzeltal): মায়া (Mayan) ভাষা। মেক্সিকোর চিয়াপাস প্রদেশে প্রায় ৩ লাখ ৭২ হাজার মানুষ এ ভাষায় কথা বলে। এ ভাষার সঙ্গে টিজটজিল (Tzotzil) ভাষার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। চিয়াপাসের লাস মার্গারেইটে এ ভাষার ওপর রেডিও অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয়।
Table of Contents
বর্ণনানুক্রমে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার বর্ণনা পর্ব ১৩
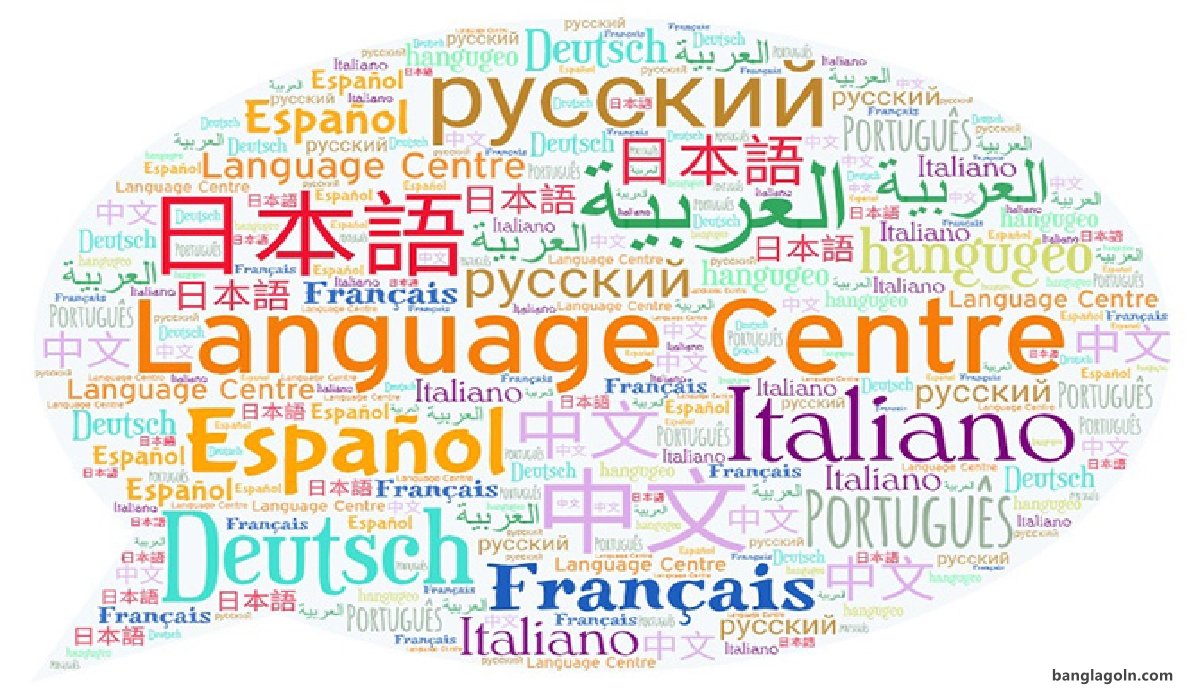
উজবেক (Uzbek)
এটি একটি তুর্কিক (Turkic) ভাষা। এ ভাষার আছে প্রায় ১ কোটি ৭০ লাখ বক্তা, তাদের বাস প্রধানত উজবেকিস্তানে। এ ভাষার প্রাথমিক রূপ চাগাতাই (Chagatai) নামে পরিচিত ছিল। (চাগতাই ছিল চেঙ্গিস খানের এক পুত্রের নাম)। এ চাগতাই লেখা হতো আরবি বর্ণমালায়। ১৯২৭ সালে আরবির পরিবর্তে ল্যাটিন বর্ণমালার ব্যবহার শুরু হয়। ১৯৪০ এ আসে সিরিলিক বর্ণমালার ব্যবহার।
উডি (Udi)
এটি উত্তর পূর্ব ককেশীয় ভাষার লেঝিয়ান (Lezgian) শাখার সদস্য। এ ভাষার ৮ হাজার বক্তার বেশিরভাগের বাস আজরবাইজানের নিজ ও কাবালা জেলায়। এর বাইরে আর্মেনিয়া, জর্জিয়া এবং রাশিয়াতেও এ ভাষার অল্প সংখ্যক বক্তা আছেন। ১৮৬৩ সালে Anton Antonovich প্রথম এ ভাষার ব্যাকরণ প্রকাশ করেন। ল্যাটিন বা সিরিলিক বর্ণমালা দিয়ে এ ভাষা লেখা হয়।
উইঘুর (Uyghur)
একটি তুর্কিক (Turkik) ভাষা। চিনের জিনজিয়াং উইঘুর অঞ্চলে প্রায় এক কোটি মানুষ এ ভাষায় কথা বলে। আফগানিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, কাজাখস্তান, কিরগিজস্তান, মঙ্গোলিয়া, তুরস্ক প্রভৃতি অঞ্চলেও উইঘুরভাষী মানুষ আছে। উইঘুর ভাষাটি ব্যুৎপত্তিগতভাবে ওরখোন (Orkhon) লিপি দ্বারা লেখা হয়েছিল যা সোগদিয়ান (Sogdian) লিপি হতে উদ্ভুত।
৮-১৬ শতক পর্যন্ত উইঘুর ভাষা সোগদিয়ান লিপি হতে উদ্ভুত বর্ণমালা ব্যবহার করে লেখা হত। একে বলা হয় ওল্ড উইঘুর। সোগদিয়ান লিপিতে ডান থেকে বামে লেখার নিয়ম থাকলেও ওল্ড উইঘুর লেখা হতো বাম হতে ডান দিক বরাবর। ১৬-২০ শতক পর্যন্ত উইঘুর আরবির একটি পরিমার্জিত বর্ণমালা ব্যবহার করে লেখা হতো।
২০ শতক থেকে উইঘুর লেখার জন্য ল্যাটিন-সিরিলিক বর্ণমালা ব্যবহারের প্রচলন হয়। তবে তা জনপ্রিয় হয়নি। এ কারণে ১৯৮৭ সালে চীনে উইঘুর লেখার জন্য পুনরায় আরবি বর্ণমালা ব্যবহারের প্রচলন হয়।
ইউক্রেনিয়ান (Ukrainian)
ইউক্রেনিয়ান একটি ইস্টার্ন স্ল্যাভোনিক (Eastern Slavonic) ভাষা। এ ভাষা রুশ ও বেলারুশীয় ভাষার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। ইউক্রেন এবং অন্যান্য কিছু দেশ যেমন, আর্জেন্টিনা, আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, বেলারুশ, ব্রাজিল, কানাডা, এস্তোনিয়া, জর্জিয়া, হাঙ্গেরি, কাজাখস্তান প্রভৃতি অঞ্চলে প্রায় ৫ কোটি ১০ লাখ মানুষ এ ভাষা ব্যবহার করে।
৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে ইউক্রেনিয়ান ভাষা ধর্মীয় কাজে ব্যবহৃত হতো। বাইবেলের ইউক্রেনিয়ান অনুবাদ লেখা হয়েছিল ‘ওল্ড স্ল্যাভোনিক’ (Old Slavionic) লিপিতে। ইউক্রেন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশের অধীনে ছিল। এ কারণে ইউক্রেনিয়ান ভাষা অনেক সময় নিষিদ্ধ ছিল।
উর্দু (Urdu)
উর্দু একটি ইন্দো-আর্য (Indo-Aryan) ভাষা। এ ভাষা প্রায় ১০ কোটি ৪০ লাখ মানুষ ব্যবহার করে। উর্দু পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা এবং হিন্দির সঙ্গে এ ভাষার প্রচুর মিল খুঁজে পাওয়া যায়। যদিও উর্দুর অনেক শব্দ ফারসি ও আরবি থেকে এসেছে কিন্তু হিন্দির বেশিরভাগ শব্দই সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত।
ভাষাবিদগণ মনে করেন, উর্দু ও হিন্দি উভয়ই খারি বোলি (Khari Boli) উপভাষা হতে উদ্ভুত। উর্দু পাকিস্তান ছাড়াও আফগানিস্তান, বাহরাইন, ফিজি, জার্মানি, ভারত, মালায়, নেপাল, ওমান, কাতার, সৌদি আরব, জাম্বিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে ব্যবহার হয়। ১২ শতক থেকে উর্দু পার্সো-অ্যারাবিক (Perso-Arabic) লিপিতে লেখা হয়।
উগারিটিক (Ugaritic)
এটি একটি সেমেটিক ভাষা। খৃষ্টের জন্মের বহুকাল আগে সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলে প্রচলিত ছিল এ ভাষা। এ অঞ্চলের একটি শহর উগারিট (Ugarit) এ ব্যবহৃত হত এ ভাষা। খৃষ্টপূর্ব ১৪ শতকে এ ভাষা বিকশিত হয়েছিল এবং খৃষ্টপূর্ব ১৮০/৭০ অব্দে এ ভাষা বিলুপ্ত হয়ে যায়।
ভোটিক (Votic)
এটি একটি ফিনিক (Finnic) ভাষা। রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবুর্গের কিংগিসেপ জেলার ক্রাকোলেয় ও লুকিংসি গ্রামের মাত্র ২০ জন মানুষ এ ভাষায় কথা বলেন। ভাষাটিকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য একটি স্কুলে তরুণদের এ ভাষা শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। এ ভাষা এস্তোনিয়ান ভাষার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। ল্যাটিন এবং সিরিলিক বর্ণমালা ব্যবহার করে এ ভাষা লেখা হয়।
ভেনডা (Venda)
ভেনডা (Venda) দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যতম সরকারি ভাষা। এ ভাষা বান্টু (Bantu) ভাষাগোত্রের সদস্য। দক্ষিণ আফ্রিকার লিমপোপো প্রদেশে প্রায় ১০ লাখ মানুষ এবং জিম্বাবুয়েতে প্রায় ১ লাখ ৫০ হাজার মানুষ এ ভাষা ব্যবহার করে।
ভেনেসিয়ান (Venetian):
এটি রোমানস (Romance) ভাষা। ভেনিস ও আশপাশের অঞ্চল যেমন, ক্রোয়েশিয়া, স্লোভেনিয়া, মেক্সিকো ও ব্রাজিলে প্রায় ২০ লাখ মানুষ এ ভাষায় কথা বলে। ইতালিয়ান ভাষার চেয়ে ফরাসি ও স্প্যানিশ ভাষার সঙ্গে এ ভাষার সাদৃশ্য বেশি। ৯-১৮ শতক পর্যন্ত যখন ভেনিস একটি স্বাধীন প্রজাতন্ত্র ছিল তখন ভেনেসিয়ান ভাষা ছিল সরকারি ভাষা।
ইতালির জাতীয় ভাষা তুসকান (Tuskan) উপভাষার কারণে ভেনেসিয়ান তার জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা হারায়। তবে ব্রাজিলের কিছু অঞ্চলে এখনও পর্তুগিজের সঙ্গে সঙ্গে ভেনেসিয়ান ভাষার তালিয়ান (Talian) উপভাষা সহ-সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃত।
ভেপস (Veps)
ভেপস একটি ফিনিক (Finnic) ভাষা। রাশিয়া, রিপাবলিক অব কারেলিয়া ও ভোলোগদা ওবলাস্টে প্রায় ৬০০০ মানুষ এ ভাষা ব্যবহার করে। এর তিনটি উপভাষা আছে: নর্দার্ন ভেপস যা লেক ওনেগায় ব্যবহৃত হয়; সেন্ট্রাল ভেপস যা সেন্ট পিটার্সবার্গ ও ভোলোগদা ওবলাস্টে ব্যবহৃত হয় এবং সাউদার্ন ভেপস যা সেন্ট পিটার্সবার্গ অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়। ২০ শতকের প্রথম দিকে ভেপস ভাষার স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেন্ট্রাল ভেপসের ওপর ভিত্তি করে ভেপসের লিখন পদ্ধতি প্রচলিত।
ভিয়েতনামিজ (Vietnamese)
অস্ট্রো-এশিয়াটিক (Austro-asiatic) ভাষা। ভিয়েতনামে প্রায় ৮ কোটি ২০ লাখ মানুষ এ ভাষায় কথা বলে। যুক্তরাষ্ট্র, চীন, কম্বোডিয়া, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা প্রভৃতি অঞ্চলেও ভিয়েতনামিজ মানুষ আছে। ১৯৫৪ সালে স্বাধীনতার পর হতে ভিয়েতনামিজ ভিয়েতনামের সরকারি ভাষা হিসেবে গৃহীত হয়। ভিয়েতনামিজ ভাষা ব্যুৎপত্তিগতভাবে সিনিফর্ম (Siniform) বর্ণমালায় লেখা হয়। এ ভাষার বহু শব্দ চাইনিজ ভাষা হতে উদ্ভূত।
এ ভাষার বৃহত্তম সাহিত্য সৃষ্টির নাম “Kim van kieu (the tale of kieu)”। বিশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত ভিয়েতনামিজ ভাষা লেখার জন্য সিনিফর্ম লিপি ব্যবহার হতো। ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত হো চি মিন বিশ্ববিদ্যালয়ে এ লিপি পাঠ্য ছিল। ১৭ শতকে রোমান ক্যাথলিকগণ ভিয়েতনামিজের জন্য একটি ল্যাটিনভিত্তিক বানান পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। বর্তমানে এই বানান পদ্ধতি ভিয়েতনামিজ লেখার জন্য ব্যবহৃত হয়।
ভোরো (Voro)
ভোরো ভাষা ফিনো-উজরিক (Finno-Ugric) ভাষাগোত্রের ফিনিক (Finnic) শাখার অন্তর্গত। এস্তোনিয়াতে প্রায় ৭০,০০০ মানুষ এ ভাষা ব্যবহার করে। সরকারিভাবে এ ভাষাকে এস্তোনিয়ান ভাষার উপভাষা হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তবে এ ভাষার নিজস্ব সাহিত্যকর্মও অপ্রতুল নয়।
উনিশ শতকে ডোরো ভাষা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল কিন্তু ১৯৮০ সালের দিকে এ ভাষার পুনর্জাগরণ ঘটে। বর্তমানে বিভিন্ন স্কুলে ভোরো ভাষা পাঠ্যঅন্তর্ভুক্ত। এস্তোনিয়াতে মাসে দুবার ভোরো সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। এ ভাষায় নাটক, কবিতা ও গল্পও রচনা হয়। ১৬৮৬ সালে নতুন টেস্টামেন্টের অনুবাদের জন্য সর্বপ্রথম ভোরো ভাষার লিখন পদ্ধতির প্রবর্তন হয়।

ওয়াখি (Wakhi)
ওয়াখি ইরানিয়ান (Iranian) ভাষাগুলোর সাউদার্ন পামির (Sonthern pamir) ভাষাগোত্রের সদস্য। আফগানিস্তান, পাকিস্তান, তাজিকিস্তান এবং চীনে প্রায় ৩১০০ মানুষ এ ভাষায় কথা বলে। ওয়াখিভাষীদের ওয়াখি বা পামিরি বলা হয়। পাকিস্তানে রেডিও-টেলিভিশনে ওয়াখি ভাষার ব্যবহার আছে। পূর্বে এ ভাষা আরবি ও সিরিলিক বর্ণমালা ব্যবহার করে লেখা হতো। বর্তমানে ওয়াখি ভাষা লেখার জন্য ল্যাটিন বর্ণমালা ব্যবহৃত হয়।
ওয়ালুন (Walloon)
একটি রোমানস (Romance) ভাষা। ওয়ালুনিয়া (দক্ষিণ বেলজিয়াম) ও ব্রাসেলসে প্রায় ১০ লাখ মানুষ এ ভাষা ব্যবহার করে। অষ্টম ও দ্বাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে পৃথক ভাষা হিসেবে ওয়ালুনের পরিচিতি ঘটে এবং ১৫ শতকে এ ভাষার লিখন পদ্ধতির প্রবর্তন হয়। বেলজিয়ামে এ ভাষার কোনো স্বীকৃতি নেই। ওয়ালুনিয়াতে অধিকাংশ মানুষ এ ভাষা বুঝতে পারলেও খুব অল্প কয়েকজনই এ ভাষা লিখতে ও বলতে পারে।
ওয়ার্লপিরি (Warlpiri)
ওয়ার্লপিরি (Warlpiri) পামা-নাইয়ুনগান (Pama-Nyungan) ভাষাপরিবারের ইয়াপা (Yapa) গোত্রের সদস্য। অস্ট্রেলিয়ার নর্দার্ন টেরিটোরিতে প্রায় ৩০০০ মানুষ এ ভাষায় কথা বলে। ওয়ার্লপিরি ল্যাটিন বর্ণমালা ব্যবহার করে লেখা হয়।
ওয়ারেই-ওয়ারেই (Waray-Waray)
মালায়ো পলিনেসিয়ান (Malayo-Polynesian) ভাষাগোত্রের ভিসায়ান (Visayan) শাখার অন্তর্গত। ফিলিপাইনের সামার, নর্দার্ন সামার, ইস্টার্ন সামার, লেইটে ও বিলিরান প্রদেশে প্রায় ৩০ লাখ মানুষ এ ভাষা ব্যবহার করে।
ওয়েইয়ু (Wayuu)
মায়পুরিয়ান (Maipurean) ভাষাগোত্রের সদস্য। ভেনিজুয়েলার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল এবং কলম্বিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে প্রায় ৩ লাখ ৫ হাজার মানুষ এ ভাষা ব্যবহার করে। বিভিন্ন স্কুলে ওয়েইয়ু স্প্যানিশ ভাষার সাথে পড়ানো হয়। তবে ১ শতাংশেরও কম সংখ্যক মানুষ এ ভাষা লিখতে-পড়তে জানে।
উইরাদজুরি (wiradjuri)
পামা-নিয়ুনগান (Pama-Nyungan) ভাষাপরিবারের উইরাদজুরি (wiradjuri) গোষ্ঠীর সদস্য। অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলসের দক্ষিণ অঞ্চলে প্রায় ১০০০ মানুষ এ ভাষা ব্যবহার করে। ১৯৮১ সালে এ উইরাদজুরিভাষী লোকসংখ্যা ছিল তিনজন। ২০০৯ সালে উইরাদজুরি ভাষী কোনো মানুষ খুঁজে পাওয়া যায়নি।
১৯৮৮ সালে উইরাদজুরি কাউন্সিল অব এল্ডার্স কর্তৃক এ ভাষা লেখার জন্য একটি আদর্শ বানান পদ্ধতি প্রণীত হয়। বর্তমানে নিউ সাউথ ওয়েলসে পার্কস ফর্ব শহরে এ ভাষা শেখানো হয়। এখানে প্রায় ১০ শতাংশ মানুষ এখন এ ভাষায় কথা বলতে পারে।
ওলোফ (Wolof)
নাইজার কঙ্গো (Niger-Congo) ভাষাগোত্রের সেনেগামবিয়ান (Senegambian) শাখার অন্তর্গত। সেনেগাল, ফ্রান্স, গাম্বিয়া, গিনি, গিনি বিসাউ, মালি এবং মৌরিতানিয়াতে প্রায় ৭০ লাখ মানুষ এ ভাষা ব্যবহার করে। সেনেগালের ৬টি জাতীয় ভাষার মধ্যে ওলোফ অন্যতম। সর্বপ্রথম ওলোফ ভাষা আরবি বর্ণমালা ব্যবহার করে লেখা হতো। সেনেগালের কিছু বৃদ্ধ মানুষ এখনো এই পদ্ধতি ব্যবহার করেন। ১৯৭৪ সাল থেকে গুলোফ ভাষা লেখার জন্য ল্যাটিন বর্ণমালা প্রণীত হয়।
ওয়াইয়ানডট (Wyandot)
ওয়াইয়ানডট (Wyandot) একটি ইরোকুয়োইয়ান (Iroquoian) ভাষা। প্রধানত যুক্তরাষ্ট্রের ওকলাহোমা ও কানাডার কিউবেকে ওয়াইনডট জনগোষ্ঠী এ ভাষা ব্যবহার করে। ঐতিহ্যগতভাবে ওয়েনডাটের (Wendat) একটি উপভাষা হলো ওয়াইয়নডট। বিশ শতকের প্রথমার্ধে এ ভাষা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, তবে বর্তমানে এ ভাষার পুনর্জাগরণের জন্য প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।
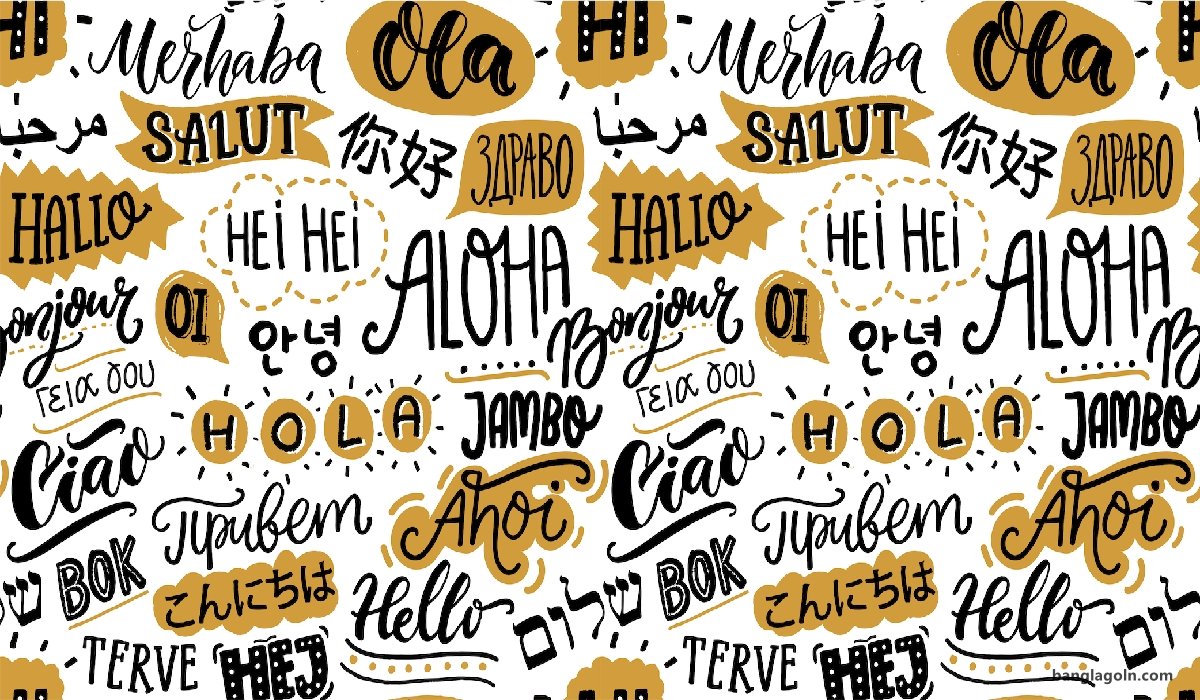
ঝোসা (Xhosa)
বান্টু (Bantu) ভাষাগোত্রের সদস্য। দক্ষিণ আফ্রিকার ইস্টার্ন কেপ প্রদেশ, অরেঞ্জ ফ্রি প্রদেশ, চিসবোই ও ট্রান্সবোইতে প্রায় ৭৯ লাখ মানুষ এ ভাষা ব্যবহার করে। ঝোসা দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারি ভাষাগুলোর মাঝে অন্যতম। এ ভাষা জুলু, সোয়াতি ও এনডিবেলে ভাষার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। উনিশ শতকের প্রথমভাগে খ্রিস্টান মিশনারিগণ ঝোসা ভাষা লেখার জন্য ল্যাটিন বর্ণমালা প্রণয়ন করেন। ১৮৩৪ সালে এ ভাষার প্রথম ব্যাকরণ বই প্রকাশিত হয়।
জ্যামট্যাংগা (Xamtanga)
এটি একটি সেন্ট্রাল কুশিটিক (Central Cushitic) ভাষা। প্রধানত ইথিওপিয়াতে ২ লাখ ১৩ হাজার মানুষ এ ভাষায় কথা বলে। এ ভাষা চামতা, খামতাঙ্গা, জামতা, খামির ইত্যাদি নামে পরিচিত। ইথিওপিক (Ethiopic) বর্ণমালা ব্যবহার করে এ ভাষা লেখা হয়।
জু (Xoo)
এটি একটি খোইসান ভাষান (Khoisan)। ভাষাটি সাসি (Tsasi) বা টা (Taa) নামেও পরিচিত। বতসোয়ানার প্রায় সাড়ে চার হাজার মানুষ এ ভাষায় কথা বলেন। নামিবিয়ায় আছেন আরও কয়েকশ বক্তা। বলা হয়ে থাকে এ ভাষায় রয়েছে সবথেকে বেশি মূলধ্বনি (Phonemes)। এ ভাষায় আছে কমপক্ষে ৮৭টি ব্যাঞ্জনবর্ণ এবং, ২০টি স্বরবর্ণ এবং ২টি স্বর। ধারণা করা হয়, এত বেশি বর্ণ আর কোন ভাষার নেই। এ ভাষার অনেকগুলো উপভাষা আছে।
জেরেনতে (Xernte)
এটি ব্রাজিলের একটি Macro-Ge, Ge-kaingang ভাষা। রিও দো সোনো এবং রিও টোকানটিনস এর মধ্যবর্তী টোকানটিনস অঞ্চলের প্রায় ১৮১০ জন মানুষ এ ভাষায় কথা বলেন। এ ভাষা লেখা হয় ল্যাটিন বর্ণমালা ব্যবহার করে। জিবে (Xibe) এটি চীনে প্রচলিত, অলটায়িক (Altaic) ভাষা পরিবারের একটি সদস্য।
এ ভাষা সিবো, সিবিন, সিবে নামেও পরিচিত। চীনের জিনজিয়াং উইঘুর, হুয়োশেং, গোংলিউ প্রভৃতি অঞ্চলে ব্যবহৃত হয় এ ভাষা। প্রায় ৩০ হাজার মানুষ এ ভাষায় কথা বলেন। মঙ্গোলিয় লিপির একটি ভার্সন দিয়ে এ ভাষা লেখা হয়। এ ভাষার নিজস্ব ব্যাকরণ এবং অভিধান আছে।
ইউরোক (Yurok)
ইউরোক একটি আদিবাসী রেড ইন্ডিয়ান ভাষা। উত্তর ক্যালিফোর্নিয়াতে সর্বোচ্চ এক ডজন বুড়ো মানুষ এ ভাষায় কথা বলে। ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূলের ডেল নর্টে হামবোল্ডট কাউন্টিতে ইউরোবা আদিবাসী গোত্রের মানুষ এ ভাষায় কথা বলত। বর্তমানে এ গোত্রের জনগণ ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করে। যা হোক, এ ভাষা পুনরুদ্ধারের জন্য প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।
ইউরোক নামটি এসেছে কারুক’ শব্দ হতে। ইংরেজিতে এর অর্থ ডাউন রিভার (Down river), ইউরোকরা নিজেদের বলে ‘পুলিকলাহ’। এর তার্থ ডাউনরিভার পিপল (Downriver people)। ইউরোক ভাষার অপর নাম উইটসপেকান। এটি উইয়ট ভাষার সঙ্গে সম্পর্কিত।
ইউপিক (Yupik)
ইউপিক ভাষা এসকিমো ভাষাগোত্রের ইউপিক শাখার সদস্য। আলাস্কা ও সাইবেরিয়ায় ১১,৮০০ জন মানুষ এ ভাষায় কথা বলে। ইউপিক ভাষা আলাস্কায় ল্যাটিন বর্ণমালা ও সাইবেরিয়ায় সিরিলিক বর্ণমালা ব্যবহার করে লেখা হয়। উনিশ শতকের প্রথম দিকে খ্রিস্টান মিশনারি এবং তাদের ইউপিক ভাষী সহযোগীরা মিলে ল্যাটিন বর্ণমালা ব্যবহার করে ইউপিক ভাষা লেখার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। এই বর্ণমালা মিশনারিদের একজন, রেভারেন্ড জন হিলঞ্জের নামানুসারে পরিচিত হয় এবং বাইবেল এবং অন্যান্য ধর্মীয় শিক্ষার ইউপিক অনুবাদ প্রকাশিত হয়।
সাইবেরিয়াতে ভাষাবিজ্ঞানীরা সিরিলিক বর্ণমালা ব্যবহার করে ইউপিক ভাষার লিখন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। তবে যেসব ইউপিক মানুষ লিখতে জানে, তারা রুশ ভাষায় লিখতে পছন্দ করে। ১৯৬০ সালে একদল ভাষাবিজ্ঞানী এবং কিছু স্থানীয় ইউপিক ভাষী মানুষ ইউনিভার্সিটি অব আলাস্কাতে একত্রে মিলে ইউপিক ভাষার জন্য একটি নতুন বর্ণমালা তৈরি করেন। তাদের অনেক লক্ষ্যের একটি ছিল, এমন একটি বর্ণমালার উদ্ভাবন করা যা কোন ‘কার’ চিহ্ন ছাড়াই ইংরেজি কিবোর্ডে বসানো যায়। নির্দিষ্ট শব্দগুলো পৃথক পৃথক বর্ণ দ্বারা প্রকাশ করাও তাদের লক্ষ্যের অন্তর্গত ছিল।